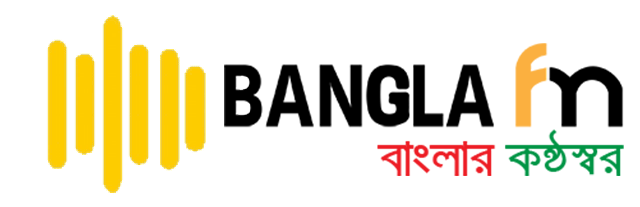বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, বিশেষ করে রাস্তা অবরোধ, কোনো হঠকারী আচরণ নয়—এটি আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে নিরাপদ সড়ক বা কোটা সংস্কার আন্দোলন—প্রতিবারই শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমেছে তখন, যখন আর কোনো পথ খোলা ছিল না।
২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, মাত্র দুজন শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সারাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। একই বছরের কোটা সংস্কার আন্দোলন একটি প্রথাগত নিয়োগ নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল এবং পরে সেটি সংস্কারেও বাধ্য করেছিল সরকারকে। সর্বোপরি ২০২৪ সালে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং পরবর্তীতে এক দফা দাবি আন্দোলনে ৫ ই আগস্ট এই দেশের নতুন সূচনা হয়।
কিন্তু যে রাস্তাটি একসময় পরিবর্তনের প্রতীক ছিল, আজ সেই একই রাস্তা জনভোগান্তির কারণ হয়ে উঠেছে—আর তাই বিতর্কও বাড়ছে।
জনদুর্ভোগ: বাস্তবতা যা অস্বীকার করা যায় না
ঢাকার রাস্তায় এই ধরনের আন্দোলনের প্রভাব সুস্পষ্ট। বুয়েটের একসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (২০২৪) অনুযায়ী, ঢাকায় প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৩৫ ঘণ্টা যানজট হয়, যার মধ্যে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন অনেক সময় ২–৩ ঘণ্টা সময় অতিরিক্ত যোগ করে।
২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে MATS শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শাহবাগ মোড় পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় বন্ধ করে রেখেছিল, যা অ্যাম্বুলেন্স, অফিসগামী মানুষ ও পরিবহন ব্যবস্থায় বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটিয়েছিল। এর আগে জানুয়ারি ২০২৫ এ ঢাকা কলেজ এলাকায় সংঘর্ষের জেরে তিন দিনের একাডেমিক স্থগিতাদেশ আসে, যা পুরো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং আশেপাশে প্রভাব ফেলে। সাম্প্রতিককালে নার্সিং শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ আবারও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।
এইসব ঘটনা জনসাধারণের বিরক্তি তৈরি করে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো উপেক্ষা করার ফলও তাই স্পষ্ট।
তবে প্রশ্ন উঠছে পদ্ধতি নিয়ে। রাস্তাঘাট অবরোধ করে সাধারণ মানুষের যাতায়াত ব্যাহত করা, অ্যাম্বুলেন্স কিংবা কর্মজীবী মানুষকে সমস্যায় ফেলে দেয়া—এই পদ্ধতি কি আদৌ গ্রহণযোগ্য? যারা প্রতিদিনের জীবনে এমন প্রতিবাদের ফলে দুর্ভোগে পড়েন, তারা প্রায়ই বলেন, ‘ভালো কথা বলছেন, কিন্তু এইভাবে বললে আমাদের ভোগান্তি হয় কেন?’
সমাধান কোথায়?
আমরা কি এমন একটা পথ খুঁজে পেতে পারি না, যেখানে প্রতিবাদ হবে, অথচ জনদুর্ভোগ কম হবে?
ডিজিটাল প্রচারণা, স্মার্ট সিট-ইন, প্রতীকী কর্মসূচি—এই ধরনের পদ্ধতি এখন সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হচ্ছে।
অন্যদিকে, প্রশাসনেরও দায়িত্ব আছে সময়মতো শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি সাড়া দেওয়ার। যদি তারা আগেভাগেই শুনতো, তবে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করার দরকার হতো না।
কিছুটা সহমর্মিতা—উভয় দিক থেকেই
প্রতিবাদ মানেই নৈরাজ্য নয়—প্রতিবাদ অনেক সময় ন্যায়বিচারের দাবি। যখন শিক্ষার্থীরা রাস্তায় দাঁড়ায়, সেটা হয়তো জনজীবনের পথে বাধা—কিন্তু তারা হয়তো দাঁড়িয়ে আছে কিছু একটার পক্ষে: শিক্ষা, অধিকার, কণ্ঠ।
আমরা রাস্তায় প্রতিবাদ দেখলেই বিরক্ত হই। কিন্তু আমরা কি একবারও ভাবি, সেই প্রতিবাদটা কেন হলো?
শিক্ষার্থীদের কণ্ঠ যেন নিভে না যায়, আবার জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাপনও যেন ব্যাহত না হয়—এই ভারসাম্য রক্ষা করাই এখন সময়ের দাবি।
ইকবাল হাসান মাহমুদ সাজিদ
বুটেক্স প্রতিনিধি