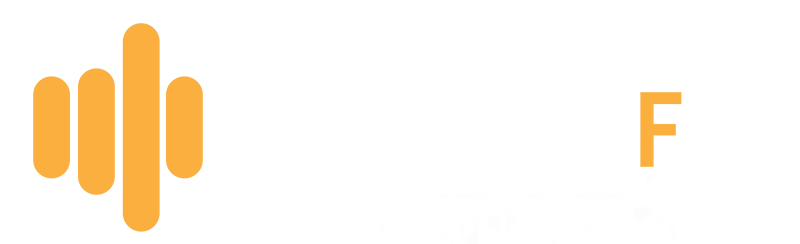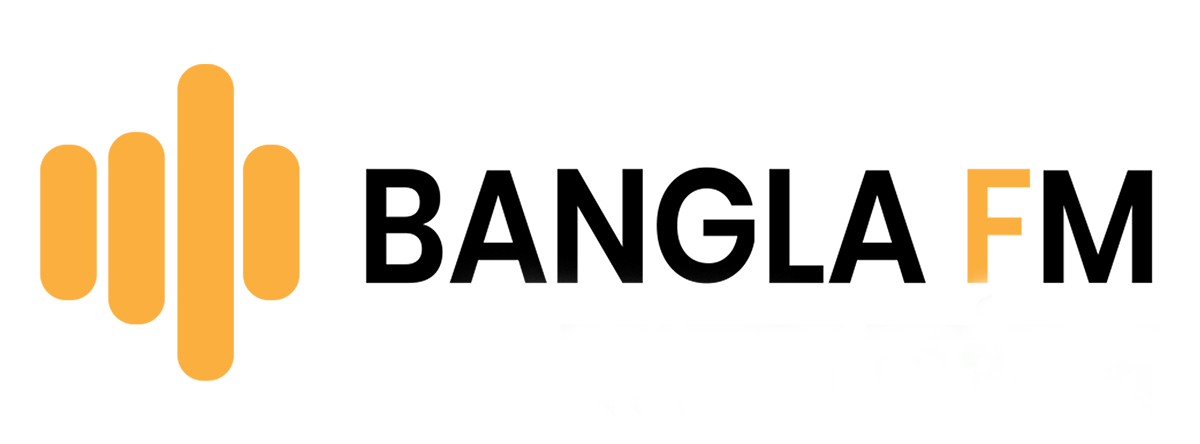যা ঘটছে, তা শুধু উদ্বেগের নয়—তা এক ভয়াবহ বাস্তবতা, যা গণমাধ্যমের আড়ালে ক্রমশ বিপজ্জনক রূপ নিচ্ছে। এক সময় সংবাদমাধ্যম ছিল মানুষের আস্থা ও তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস। কিন্তু বর্তমান সময়ের অনেক টেলিভিশন চ্যানেল ও সামাজিক মাধ্যম এই দায়িত্ব পালনে ভয়ানকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। বরং তারা হয়ে উঠেছে বিভ্রান্তি, নাটকীয়তা এবং উত্তেজনার কারখানা।
গণমাধ্যমের কাজ খবর পরিবেশন করা, খবর তৈরি করা নয়। যখন সংবাদমাধ্যম নিজেই নাট্যকার হয়ে ওঠে, তখন খবর আর খবর থাকে না—তা হয়ে ওঠে উত্তেজনার ইন্ধন। ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলির একটি বড় অংশ এখন এই কাজটিই করছে—মানুষকে উত্তেজিত করছে, বিভেদ সৃষ্টি করছে।
গণমাধ্যমের কাজ হচ্ছে তথ্য তুলে ধরা—সঠিক, যাচাইকৃত ও প্রাসঙ্গিক তথ্য। কিন্তু আজ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, মিডিয়া নিজেই হয়ে উঠেছে ‘খবর তৈরির’ যন্ত্র। বাস্তব ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে, নাটকীয় আবহে উপস্থাপন করে, সেটিকে ‘উৎসাহী প্রতিবেদন’ নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এই অতিরঞ্জনের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিকটি হচ্ছে সীমান্ত ও নিরাপত্তা বিষয়ক সংবাদ পরিবেশনে।
সম্প্রতি উরি সেক্টরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু টেলিভিশন চ্যানেলের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, তারা এমন এক যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিবেশ তুলে ধরেছে যেন গুলি পায়ের নিচে এসে পড়ছে, যেন সাংবাদিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট করছেন। বাস্তবে যদিও গুলি বিনিময় হচ্ছে সীমান্ত এলাকায়, তা সীমান্ত অতিক্রম করছে না—এবং স্থানীয় মানুষেরাও সেভাবে আতঙ্কিত নন। বরং তারা জানেন, এই সংঘাত নতুন কিছু নয়, এবং সীমান্তের জীবন এমন অনিশ্চয়তায় অভ্যস্ত।
কিন্তু টেলিভিশন পর্দায় সে বাস্তবতা নেই। আছে চিৎকার, ক্যামেরার মুভমেন্ট, ভয় ধরানো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, এবং ‘এক্সক্লুসিভ লাইভ রিপোর্ট’ নামে অতিরঞ্জিত দৃশ্যপট। এই ধরনের প্রতিবেদন বাস্তবতাকে বিকৃত করে, জনমনে অহেতুক ভয় সৃষ্টি করে, এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে।
আরও ভয়াবহ দৃষ্টান্ত দেখা গেছে পহেলগামে। সেখানে সেনাবাহিনীর অভিযান চলাকালীন কিছু মিডিয়া সরাসরি লাইভ সম্প্রচারে সেই ছবি প্রচার করেছে—যা কেবল সাংবাদিকতার নীতিবিরুদ্ধই নয়, নিরাপত্তার দিক থেকেও ভয়ানক। মনে করিয়ে দেয় ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার সময়কার সেই ভুল সিদ্ধান্ত, যেখানে টেলিভিশনে লাইভ সম্প্রচারে দেখা গিয়েছিল এনএসজি-র অভিযান। সেই ছবি সন্ত্রাসীদের হাতে পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল ছিল।
এখানে প্রশ্ন জাগে—এই ধরনের ‘রিপোর্টিং’ আদৌ কি সাংবাদিকতা? নাকি এটি এক ধরনের জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রতিযোগিতা, যেখানে সত্যের চেয়ে উত্তেজনাই বেশি বিকোয়?
প্রশ্ন উঠছে মিডিয়ার দায়বদ্ধতা নিয়ে। যখন গণমাধ্যমের একটি বড় অংশ সামাজিক দায়িত্ব ভুলে যায়, তখন তার প্রভাব পড়ে রাষ্ট্রের কাঠামোতেও। মানুষ বিভ্রান্ত হয়, বিভক্ত হয়, এবং ক্রমশ এক প্রহসনের মধ্যে আটকে পড়ে। যে মিডিয়া সত্য বলার কথা ছিল, সেই মিডিয়া যদি মানুষের আবেগকে অস্ত্র বানিয়ে রাজনৈতিক বা কর্পোরেট উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তাহলে তা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক।
ভয়াবহ দৃষ্টান্ত দেখা গেছে পহেলগামে। সেখানে সেনাবাহিনীর অভিযান চলাকালীন কিছু মিডিয়া সরাসরি লাইভ সম্প্রচারে সেই ছবি প্রচার করেছে—যা কেবল সাংবাদিকতার নীতিবিরুদ্ধই নয়, নিরাপত্তার দিক থেকেও ভয়ানক।
এই পরিস্থিতি শুধু চিন্তার নয়, ভয়ংকর। মানুষ জানে না কোনটা সত্য, কোনটা সাজানো। কেউ খবর দেখছে আতঙ্কে, কেউ উগ্রতায়। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, কূটনীতি, এমনকি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—সবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই সংবাদ-নাটকের কারণে।
গণমাধ্যমের উচিত হবে আত্মসমালোচনায় ফেরা। সংবাদ পরিবেশনের আগে বারবার নিজেকে প্রশ্ন করা—‘আমি যা বলছি, তা কি সত্য? তা কি প্রয়োজনীয়? তা কি জনস্বার্থে?’ না হলে এই ‘যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা’ একদিন সত্যিকারের যুদ্ধকে উস্কে দিতে পারে—মানসিক, রাজনৈতিক, এমনকি বাস্তবিক অর্থেই।
একটা জাতিকে সত্য জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কেবল অন্যায় নয়—তা এক ধরনের সহিংসতা।