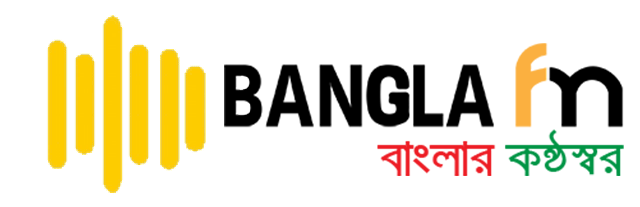যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব লেনা দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে–
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।
যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়, আহা,
ফুলের বাগান ঘন ঘাসের পরবে সজ্জা বনবাসের,
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দিঘির ধারগুলায়–
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।
তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে,
কাটবে দিন কাটবে,
কাটবে গো দিন আজও যেমন দিন কাটে, আহা,
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী এমনি সে দিন উঠবে ভরি–
চরবে গোরু খেলবে রাখাল ওই মাঠে।
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।
তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি– আহা,
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে॥
-(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটি আঠারবাড়ী জমিদার বাড়ির রানী পুকুরের ঘাটে বসে লিখেছিলেন।)
জমিদারি প্রথা বিলোপের পর এবার ৭৪ বছর পূর্ণ হয়েছে। এটি করা হয়েছিল ‘স্টেট অ্যাকুজিশন অ্যান্ড টেনান্সি অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর মাধ্যমে। কার্যকর করা হয়েছে ১৯৫১ সনের ১৬ মে থেকে।
ভারতবর্ষে জমিদারি প্রথা ছিলো বহল আলোচিত একটি ব্যবস্থা। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ইতিহাসের বিবর্তনে জমিদারি প্রথা বাঁকে বাঁকে নানা ধরনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। সমাজ বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সেই জমিদারি বিলুপ্ত হলেও তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত সেই বাড়িঘরের এখনও নিদর্শন মেলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেই জমিদারদের অনেকের জীবন-কাহিনি এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে রূপকথার কাহিনির মত। ধারণা করা হয় জমিদার ফারসি ‘যামিন’ (জমি) ও ‘দাস্তান’ (ধারণ বা মালিকানা)-এর বাংলা অপভ্রংশের সঙ্গে ‘দার’ সংযোগে ‘জমিদার’ শব্দের উৎপত্তি। মধ্যযুগীয় বাংলার অভিজাত শ্রেণির ভূমি অধিকারীদের পরিচয়ের জন্য নাম হিসেবে শব্দটি ঐতিহাসিক পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়।
মোগল আমলে জমিদার বলতে প্রকৃত চাষির ঊর্ধ্বে সকল খাজনা গ্রাহককে বোঝানো হতো।
প্রখ্যাত লেখক কমরেড বদরুদ্দীন উমর তার ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক’ গ্রন্থে প্রথম পরিচ্ছেদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্বে ‘মোগল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা’ সম্পর্কে আলোচনায় লিখেছেন ‘জমির ওপর রাষ্ট্র অথবা জমিদার জাতীয় কোন শ্রেণির দখলী স্বত্ব মোগল আমলে ছিল না। জমির সত্যিকার মালিক তখন ছিল তারাই যারা নিজেরা গ্রামে কৃষি কার্যের দ্বারা ফসল উৎপাদন করতো। সে সময় যাদেরকে জমিদার বলা হতো তারা ছিল সরকারের রাজস্ব আদায়ের এজেন্ট মাত্র, ভূস্বামী বা জমির মালিক নয়।’ সুতরাং দেখা যায় মোঘলদের সময় বা তার পূর্ববর্তী শাসনামলেও বাংলায় প্রচলিত অর্থে কোনো জমিদার ছিল না। এ ধারণায় জমিদারগণ রাজস্বের চাষি ছিল মাত্র, তারা জমির মালিক ছিল না। জমির মালিক ছিল কৃষক। সে সময় জমির মালিকদের বলা হতো রায়ত বা চাষি। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রবর্তিত এক প্রকার ভূমি ব্যবস্থা নামই হচ্ছে জমিদারি প্রথা। এই জমিদারি প্রথার অধীনে একটি অঞ্চলের বেশিরভাগ জায়গাকে জমিদারিতে ভাগ করে বছরে খাজনা প্রদানকারী এক ধরনের ভূস্বামীদের হাতে ছেড়ে দেয়া হতো। এসব ভূস্বামীরাই সমাজ ব্যবস্থায় ‘জমিদার’ নামে পরিচিত ছিল। জমিদারেরা তাদের প্রজাদের কাছ থেকে ইচ্ছা মত কর আদায় করতে পারতো। এই সুযোগ ব্যবহার করে তৎকালীন জমিদারেরা শোষণ নিপীড়নের প্রতীক হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। তারা অত্যন্ত প্রভাবশালী শ্রেণির লোক ছিলো বিধায় তাদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার সাহস কারোরই ছিলো না। অনেক সাধারণ প্রজা জমিদার শ্রেণির রোষানলে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে এলাকা ছাড়া হয়েছে এরকম উদাহরণ প্রচুর। জমিদার শ্রেণির মানুষেরা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং অর্থবিত্তের জোরে অনেক ভালো কাজ সমাজের জন্য করেছেন সত্যি। কিন্তু অনেক জমিদার তাদের শোষণ নিপীড়নের জন্য সমাজের ঘৃণার পাত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। সে শোষণের বাস্তবতা নিয়ে আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে নানা কালজয়ী নাটক, গল্প, উপন্যাস ও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।অনেকেই সে কাহিনিকে রূপকথার কল্পকাহিনি মনে করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে, সেই শোষণের ইতিহাস ছিল নির্মম। তবে এটাও সত্য যে এই জমিদার শ্রেণি থেকে সমাজ নানাভাবে উপকৃতও হয়েছে। তাদের দ্বারা এখানে শিক্ষার বিস্তার হয়েছে ব্যাপক এবং তারা নানা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডেরও বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। এ অঞ্চলের অনেক পুরানো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তাদের হাতেই গড়া। কৃষি ব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যবস্থাও জমিদার শ্রেণির ভূমিকা অগ্রগন্য। জমিদারি প্রথার প্রবর্তনের ইতিহাস থেকে জানা যায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর বাংলার মসনদে মূলত ইংরেজদের মদদপুষ্ট শাসকরা ক্ষমতায় বসে। তাদের অদূরদর্শী শাসনের ফলে বাংলায় সরাসরি ইংরেজ প্রতিনিধিরা আসতে শুরু করে গভর্নর জেনারেল রূপে। এরূপ দ্বৈত শাসনে বাংলার অর্থনীতি দ্রুতগতিতে ভেঙে পড়তে থাকে। সারাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৭৭০ সালে সারাদেশ জুড়ে ভয়াবহ মন্বন্তর শুরু হয় যা ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) নামে পরিচিত। এরপর এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পাঁচশালা বন্দোবস্তের প্রবর্তন করে ওয়ারেন হেস্টিং। হেস্টিং প্রবর্তনকৃত এই বন্দোবস্ত ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হবার ফলে খাজনা দিতে না পেরে রায়তরা জমি ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। এরপর নিয়ে আসা হয় একশালা বন্দোবস্ত। এ সময় মূলত জমির দখল পেতো হিন্দু ব্রিটিশপ্রিয় পরিবারগুলো, তারা শিক্ষা দীক্ষায় তৎকালীন সমাজে অগগ্রসরমান জনগোষ্ঠী ছিলো। অপরদিকে শোষিত হতে শুরু করে সাধারণ অনগ্রসর কৃষকরা। পাঁচশালা ও একশালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হওয়ার পর গভর্নর জেনারেল হিসেবে এদেশে আসেন লর্ড কর্নওয়ালিশ, তিনি ইংল্যান্ডের জমিদার পরিবার থেকে এসেছিলেন। তিনি অনুভব করেন রাজস্ব আদায় ঠিক রেখে ব্রিটিশ অনুগত গোষ্ঠী তৈরির জন্য জমিদার প্রথা এদেশে আনতে হবে। ১৭৯০ সালে তিনি দশশালা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন যা ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিবর্তিত হয়। জমির মালিকানা চলে যায় ইংরেজদের অনুগত গোষ্ঠীর হাতে, যারা ‘জমিদার’ বলে সম্বোধিত হতো। এভাবে ইংরেজরা তাদের এদেশীয় দোসর তৈরি করে যারা উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘস্থায়ী করতে খুব বড় ভূমিকা রেখেছিলো। জমিদারি প্রথার ফলে বাংলায় বুর্জোয়া গোষ্ঠী তৈরি হয়। এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণি প্রভূতে রূপান্তরিত হয়। জমিদাররা কৃষকের থেকে খাজনা আদায় করত, এ সময় কৃষকরা যারা এক সময় জমির মালিক ছিলেন তারা দুঃখজনক ভাবে ভূমিদাসে পরিণত হন। খাজনা আদায়ের দায়িত্ব জমিদারের নায়েব-গোমস্তার হাতে ন্যস্ত হবার ফলে জবাবদিহিতা ও অভিভাবকত্বের অভাবে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। নায়েব-গোমস্তারা ইচ্ছামত অত্যাচার চালাতো কৃষকের ওপর। সে সময় দেশজুড়ে বিদ্রোহ-আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৮৫৯-৬১ সালে নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ঐ সময় সাধারণ মানুষের জীবন কতটা ভয়ানক ছিল তার কিছুটা জানা যায় মীর মোশাররফ হোসেনের বিয়োগান্তক নাটক ‘জমিদার দর্পণ’ ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ‘নীলদর্পণ’ থেকে। এ কারণে এই নাটকগুলো তৎকালীন জমিদারদের ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালুর মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাদের করে দেয়া হলো জমির মালিক অথচ এই জমিদারেরাই একসময় ছিল খাজনা আদায়ের এজেন্ট মাত্র। এই জমিদারেরা খাজনার একটি নির্দিষ্ট অংশ ইংরেজদের কাছে পৌঁছে দিত। এর ফলে বাংলার কৃষক ও গরিব শ্রেণির ওপর নেমে আসে দেড়শত বছরের দুর্গতি। বাংলার কৃষকদের ওপর জমিদারদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের যে চিত্র তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান ছিলো তা জানলে গা শিউরে ওঠে। খাজনা দিতে না পারলে চর্মপাদুকা প্রহার, বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষঃস্থল দলন, খাপরা দিয়ে কর্ণ ও নাসিকা মর্দন, ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ, পিঠে দু’হাত মোড়া দিয়ে বেঁধে মোচড়া দেওয়া, গায়ে বিছুটি দেওয়া, হাত পা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা, কান ধরে দৌড় করানো, কাঁটা দিয়ে হাত দলন, গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রোদে ইটের উপর পা ফাঁক করে দু’হাত ইট দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা, প্রবল শীতের সময় জলে চুবানো, কারারুদ্ধ করে উপবাসী রাখা, ঘরের মধ্যে বন্ধ করে লঙ্কা মরিচের ধোঁয়া দেওয়াসহ বিভৎস ও বিকৃত এসব শাস্তি জমিদারি প্রথাকে অভিশপ্তে টেনে নিয়েছিলো।
তৎকালীন পূর্ব বাংলায় বর্তমানে বাংলাদেশে ১৯৫০ সনের পূর্বে জমিদারি প্রথা বিদ্যমান ছিল। বাঙালার জমিদারি প্রথা অতি প্রাচীন। পলাশীর যুদ্ধের আগেও সুবা বাঙালাতে জমিদাররা ছিলেন। চাষিদের থেকে আদায় করা খাজনা থেকে নিজের ভাগ রেখে বাকিটা জমা করতেন নবাবের কাছে।
ইংরাজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসার সুবিধার জন্য ‘এজেন্সি হাউস’ স্থাপন করে। সাবেক কলকাতার এক শ্রেণীর বাঙালী হিন্দু ব্যবসায়ী এজেন্সি হাউসগুলির দেওয়ান ও মুৎসুদ্দি হয়ে বিপুল পরিমান ধন-সম্পদ উপার্জন করেন। ক্রমশ এঁরা সমাজের মাথা হয়ে উঠলেন। শ্রী শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ বইতে লিখলেন, “তখন নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুই দিনে ধনী হইয়া উঠিত”।
এই ব্যবসায়ীরা উপার্জিত অর্থ-সম্পদ থেকে মুনাফা পাওয়ার জন্য শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগের ভাবনা শুরু করলেন। আর এতেই ইংরাজরা সিঁদুরে মেঘ দেখলেন। ইংরাজরা নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করে তা নিজেদের হাতে রাখতে আগ্রহী এবং সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দিতে তারা নারাজ। কিন্তু এই ধনী বাঙালী সম্প্রদায়কে ইংরাজরা কোনোভাবেই বিরূপ করতে চাইলেন না।
অন্য দিকে, সঠিক গ্রামীন পরিকাঠামো না থাকাতে কোম্পানীর সরকার জমি থেকে খাজনা আদায়ও সঠিক ভাবে করতে পারছে না। এই সুযোগে জমিদাররা প্রায়শই অল্প খাজনা দিচ্ছেন কিম্বা ফাঁকি দিচ্ছেন।
১৭৯৩ সনে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জমিদারদের বরাবরে সব জমি ‘১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের’ আওতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারি প্রথা চালু করা হয়। ওই আইন মতে সব ধরনের জমির মালিক হন জমিদাররা। জমিদারদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেওয়া এত বিশাল পরিমাণ জমি নিজের দখলে রাখিয়া ভোগদখল করা সম্ভবপর না হওয়ায় তাহারা উহা হইতে কিছু সম্পত্তি নিজেদের ভোগদখলের জন্য রাখিয়া বাদবাকি জমি বিভিন্ন রায়তের বরাবরে খাজনার বিনিময়ে বন্দোবস্ত দিয়া বন্দোবস্ত গ্রহীতাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া মালিকানা স্বত্ব বজায় রাখিতেন। বন্দোবস্ত দেওয়া জমিকে প্রজাবিলি বা রায়তি জমি এবং খাস দখলীয় জমিকে খাস জমি বলা হইত। ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে বন্দোবস্ত দেওয়া এবং খাজনা আদায়ের বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান না থাকার সুযোগে জমিদারগণ তাহাদের ইচ্ছামতো খাজনা নির্ধারণ ও আদায়ের পদক্ষেপ নেওয়াতে সাধারণ প্রজাগণ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হইতে থাকিলে ব্রিটিশ সরকার প্রজাদের রক্ষাকরণার্থে ১৮৮৫ সনে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তন করেন। ওই আইনে প্রজাদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা ছাড়াও জমিদার কর্তৃক প্রজাদের যদেচ্ছা উচ্ছেদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া আদালতে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য রেন্টস্যুট এবং শর্ত ভঙ্গের জন্য উচ্ছেদের মোকদ্দমার বিধান চালু করা হয়। ওই আইনটিকে তৎকালীন সময়ে প্রজাদের রক্ষাকবচ হিসেবে অভিহিত করা হইলেও সাধারণ প্রজাগণ অশিক্ষিত হওয়ায় আইন বিষয়ে অজ্ঞ থাকার কারণে তাহারা উক্ত আইনের ফল তেমন ভোগ করিতে পারেন নাই বরং জমিদারগণ পূর্ববৎ প্রজাদের ওপর ইচ্ছাকৃত খাজনা ধার্যে এবং আদায়ের নামে অত্যাচার ও অবিচার অব্যাহত রাখেন। এমতাবস্থায় তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশেষ করিয়া শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক,মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ জনগণকে এ মর্মে আশ্বাস দেন যে, ব্রিটিশ সরকারকে আন্দোলনের মাধ্যমে বিতাড়িত করিতে পারিলে তাহারা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদক্রমে সকল জমির রায়তদের যার যার দখলীয় ভূমির মালিক হিসেবে গণ্য করিবেন। উহারই ফলে ১৯৪৭ সনে ব্রিটিশ সরকার বিতাড়িত হইয়া পাকিস্তান ও ভারত নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের রায়তদের রক্ষার জন্য ১৯৫০ সনে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও প্রজাদের স্ব-স্ব ভূমিতে মালিকানা অর্জনের আইন পাস হয়। যাহা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ হিসেবে পরিচিত।
রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের প্রকৃতি ও প্রয়োগ:
১) প্রজাবিলিকৃত সম্পত্তি : রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনকে পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। উক্ত পাঁচটি খণ্ডের মধ্যে ১ হইতে ৪ খণ্ডে কীভাবে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদক্রমে প্রজাদের যার যার দখলীয় ভূমিতে মালিকানা স্বত্ব অর্জন করিবেন এবং জমিদারগণ তাহাদের বিশাল পরিমাণ খাস দখলীয় সম্পত্তির মধ্যে কী প্রকার ও কী পরিমাণ সম্পত্তি নিজেদের মালিকানায় ও দখলে রাখিতে পারিবেন তৎবিষয়ে বর্ণনা করা হয়। উক্ত ৪ খণ্ডে বর্ণিত ধারাগুলোর মধ্যে ধারা-৩, ধারা-৩ক, ধারা-৪, ধারা-২০, ধারা-২৩, ধারা-২৪, ধারা-৪৬ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধারা-৩-এ বলা হইয়াছে যে, জমিদারদের নিকট হইতে ধারা-৩ক এবং ধারা-৪-এর বিধানমতে নোটিস জারি অন্তে সরকার কর্তৃক জমিদারদের সেরেস্তা হইতে সংগৃহীত প্রজাবিলিকৃত সম্পত্তির তালিকাগুলো সংশ্লিষ্ট জমিদারদের নাম এবং প্রজাবিলিকৃত সম্পত্তি বিবরণ দিয়ে গেজেট আকারে প্রকাশ করিবেন। উক্ত প্রকাশিত গেজেটটি পরবর্তীতে প্রজাবিলি সম্পত্তির গেজেটরূপে পরিচিতি লাভ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রজাবিলিকৃত সম্পত্তিতে জমিদারদের কোনো ভোগ-দখলের অধিকার ছিল না। উহাতে শুধুমাত্র খাজনা নেওয়ার অধিকার বিদ্যমান ছিল। উক্ত প্রজাবিলি গেজেটে উল্লিখিত প্রজাবিলিকৃত সম্পত্তিতে সাবেক জমিদারদের খাজনা নেওয়ার অধিকার সরকার কর্তৃক হুকুমদখলের মাধ্যমে নিজে গ্রহণের জন্য এবং স্ব-স্ব প্রজাদের দখলীয় ভূমিতে মালিকানা ঘোষণার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণী তালিকা (সিএ রোল) প্রস্তুত করার পর তালিকায় নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের টাকা স্ব-স্ব জমিদারদের বরাবরে প্রদানান্তে উক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা সংশ্লিষ্ট জমিদারকে প্রদত্ত হইয়াছে মর্মে ঘোষণাপূর্বক সরকার ৪৬ ধারায় অপর আরেকটি গেজেট প্রকাশ করেন, যাহা পরবর্তীতে ক্ষতিপূরণ প্রদান গেজেট হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এভাবে দুইটি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সরকার প্রজাবিলিকৃত সম্পত্তিতে জমিদারদের জমিদারি তথা খাজনা নেওয়ার অধিকার চিরতরে বিলীন করিয়া স্ব-স্ব প্রজাদের স্ব-স্ব প্রজাবিলিকৃত সম্পত্তিতে মালিকানা ঘোষণা এবং সরকার পূর্বের জমিদারদের পরিবর্তে নিজে প্রজাইস্বত্বে মালিকদের নিকট হইতে খাজনা নেওয়ার অধিকার গ্রহণ করেন।
২) জমিদারদের খাস দখলীয় সম্পত্তি : অন্যদিকে প্রজাবিলিকৃত সম্পত্তি বাদে জমিদারদের খাস দখলে থাকা বিশাল পরিমাণ জমিকে ২০ ধারার বিধানমতে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। উহাদের মধ্যে একটি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণীয় সম্পত্তি (Compulsory acquirable property) যেমন- খাল, বিল, নদী-নালা, পথ-ঘাট, বন, হাট-বাজার, কাচারি ইত্যাদি। ওইরূপ বাধ্যতামূলক হুকুম দখলি সম্পত্তি বাদে বাদবাকি যে পরিমাণ জমি জমিদারের দখলে অবশিষ্ট থাকে উহাকে পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। উহাদের মধ্যে ৩৭৫ বিঘা পরিমাণ ভূমিকে রিটেইনেবল এবং বাদবাকি খাস দখলি ভূমিকে নন-রিটেইনেবল সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। সরকার জমিদারকে বাধ্যতামূলক হুকুম দখলি ভূমি বাদে যার যার খাস দখলে থাকা বাদবাকি ভূমির মধ্যে কোন ৩৭৫ বিঘা ভূমি নিজ মালিকানায় রাখিবেন তৎমর্মে অপশন বা স্বাধীনতা দিয়ে চয়েজ তালিকা দেওয়ার জন্য বলেন। জমিদারগণ সরকারের চাহিদা মতে ৩৭৫ বিঘা জমির চয়েজ তালিকা দিলে সরকার পরবর্তীতে উহাতে জমিদারদের মালিকানা ঘোষণাপূর্বক এসএ খতিয়ান প্রস্তুত ও প্রকাশে উহাতে মালিকানা অর্জনের ভিত্তি হিসেবে মন্তব্যের কলামে ২৩/১ ধারা বা চয়েজমূলে মালিকমর্মে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে প্রজাবিলিকৃত সম্পত্তির বিপরীতে প্রস্তুতকৃত সংশ্লিষ্ট এসএ খতিয়ানকে মালিকানার ভিত্তি হিসেবে ২৪/১ ধারা হিসেবে উল্লেখ করেন। এভাবে জমিদারদের দখলে থাকা ৩৭৫ বিঘার অতিরিক্ত বাদবাকি সমস্ত নন-রিটেইনেবল খাস ল্যান্ড সরকারের খাস সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হইয়া সরকারের নামে ১নং এসএ খতিয়ানে রেকর্ড হয়। এভাবে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকরীক্রমে আক্রোসে সরকার জমিদারদের নন-রিটেইনেবল সম্পত্তিতে, সাবেক জমিদারগণ স্ব-স্ব রিটেইনেবল সম্পত্তিতে এবং প্রজাগণ স্ব-স্ব দখলি সম্পত্তিতে যার যার মতো মালিক হিসেবে গণ্য হন এবং জমিদার এবং প্রজা যার যার স্ট্যাটাস পরিবর্তন করিয়া সকলেই সরকারের অধীনে নামমাত্র হারে খাজনা প্রদানের শর্তে সাধারণ এক শ্রেণির রায়তরূপে পরিণত হন।
৩) পি.ও ৯০/১৯৭২ : সরকার ১৯৫০ সনে শুধুমাত্র জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও প্রজাদের মালিকানা ঘোষণার আইন প্রবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং ওইরূপ আইন প্রয়োগে বা কার্যকরীতে সাবেক জমিদার বা জমিদারদের প্রতিনিধি বা অন্য কোনো ব্যক্তি যাহাতে আদালতে বা অন্য কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় দরখাস্ত, মামলা মোকদ্দমা দায়েরে কোনোরূপ বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য পি.ও ৯০/১৯৭২ জারি করত ঘোষণা করেন যে, প্রজাবিলি গেজেটে উল্লিখিত সম্পত্তিতে জমিদারদের জমিদারি বা খাজনা নেওয়ার অধিকার হুকুমদখল প্রক্রিয়াকে প্রশ্ন বা চ্যালেঞ্জ করিয়া কেহ কোনো আদালতে কোনো প্রকার মামলা-মোকদ্দমা রুজু করিতে পারিবে না। মামলা-মোকদ্দমা দায়ের বিষয়ে ওইরূপ নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কেহ ডযড়ষব ংধষব অপয়ঁরংরঃরড়হ কে চ্যালেঞ্জ করিয়া কোনো মামলা করিয়া থাকিলে বা কোনো মামলা চলমান থাকিলে মামলাগুলো তাৎক্ষণিক খারিজ হইবে। উক্ত পি.ও ৯০/১৯৭২ তে আরও বলা হয় যে, পি.ও ৯০/১৯৭২ জারির পূর্বে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করিয়া কোনোরূপ আদেশ, নিষেধাজ্ঞা বা ডিক্রি কোনো আদালত হইতে পাইয়া থাকিলে সেইগুলো অবৈধ, বেআইনি ও অকার্যকর মর্মে গণ্য হইবে।
৪) ১৯৫০ সনের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তনের পর সরকারি সংস্থা কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর তত্ত্বাবধানে থাকা জমিদারদের সম্পত্তির আইনগত অবস্থা : ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, ১৯৫০ সনে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন এবং প্রজাদের যার যার দখলি সম্পত্তিতে মালিকানা ঘোষণা বিষয়ক আইন প্রবর্তনের পূর্বে সকল জমির মালিক ছিলেন জমিদারগণ। তৎকালীন সাবেক জমিদারদের মধ্যে ঢাকার জমিদার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর এবং গাজীপুরের জমিদার কুমার রবীন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী তাহাদের স্ব-স্ব সম্পত্তি দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিতে অপারগ হওয়ায় তাহাদের স্ব-স্ব সমুদয় সম্পত্তি ১৮৭৯ সনে প্রবর্তিত কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইনের বিধানমতে জমিদারদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে গঠিত সরকারি সংস্থা ‘কোর্ট অব ওয়ার্ডস’ গ্রহণ করে এবং তাহাদের পক্ষে তাহাদের সকল প্রকার সম্পত্তি দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিতে থাকে। উক্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, সরকারি সংস্থা কোর্ট অব ওয়ার্ডস বা সরকার প্রাক্তন জমিদারদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যে সকল সম্পত্তি দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করিবেন সেই সকল সম্পত্তিতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বা সরকার কখনও মালিক হইবে না। কেবলমাত্র জমিদারদের তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক হিসেবে উহা রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী হইবেন ও থাকিবেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইন-এর আওতায় তত্ত্বাবধানে নেওয়া সাবেক জমিদারদের সম্পত্তির আয় হইতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস প্রথমে সরকারি ভূমি উন্নয়ন কর, তৎপর ব্যবস্থাপনা খরচ প্রদান বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা জমিদার বা তাহাদের ওয়ারিশান বা ওয়ার্ডসদের বরাবরে হিস্যা অনুপাতে বিভাগ বণ্টনকরতঃ প্রদান করিতে হইবে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস উহার তত্ত্বাবধানে থাকা সম্পত্তির আয় যেমন ভোগ করিতে পারেন না তেমনি উহার কোনো আয় সরকারের ফান্ডেও জমা হইবে না। এক কথায় কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর তত্ত্বাবধানে থাকা প্রাক্তন জমিদারদের রিটেইনেবল সম্পত্তিতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস কখনও মালিকানা স্বত্ব অর্জন করিতে পারিবে না। উহার মালিক পূর্ববৎ কোর্ট অব ওয়ার্ডসই থাকিয়া যাইবে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস কেবলমাত্র জমিদারদের পক্ষে তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে উক্ত রিটেইনেবল সম্পত্তি দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন। ১৮৭৯ সনের কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইনের বিধানমতে গঠিত সরকারি সংস্থা কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর তত্ত্বাবধানে থাকা প্রাক্তন জমিদারদের দখলে থাকা রিটেইনেবল সম্পত্তি ও প্রজাদের দখলে থাকা প্রজাবিলিকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১৯৫০ সনের জমিদারি প্রথা ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রযোজ্য হইবে কি না প্রশ্ন উঠিলে দেশের তৎকালীন পার্লামেন্ট ১০/৫২নং আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে ‘কোর্ট অব ওয়ার্ডস’ আইনে নতুনভাবে ৮(এ) ধারা সংযোজনে ঘোষণা করেন যে, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনটি কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর তত্ত্বাবধানে থাকা প্রাক্তন জমিদারদের উভয় প্রকার সম্পত্তির ক্ষেত্রেও একইরূপ প্রযোজ্য হইবে। উক্ত ৮(এ) ধারাতে বলা হয় যে, ১৯৫০ সনের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের আওতায় হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি বাদে কোর্ট অব ওয়ার্ডস শুধুমাত্র রিটেইনেবল বাদবাকি খাস দখলি সম্পত্তি দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন।
৫) কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর অধীনে থাকা জমিদারদের প্রজাবিলি গ্যাজেটে উল্লিখিত সম্পত্তিতে প্রজাদের মালিকানা অর্জনের সমর্থনে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের প্রদত্ত রায় : ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকরীক্রমে যথাক্রমে- সরকার, পূর্বের জমিদার এবং জমিদারদের অধীনে থাকা প্রজাদের মালিকানা অর্জন হওয়ার বিষয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়গুলোর মধ্যে ৩৩ ডিএলআর-এ ১৩ পৃষ্ঠায়, ১৪ এমএলআর-এ ৪০১ পৃষ্ঠায়, ১৯ এমএলআর-এ ১ পৃষ্ঠায়, ৩৭ বিএলডিতে ৪৮০ পৃষ্ঠায় এবং ৫ সিএলআর-এ ৩১৩ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত রায়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
উক্ত রায়গুলোতে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ ইতঃপূর্বে উল্লিখিতমতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বিধান কার্যকরীক্রমে কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর তত্ত্বাবধানে থাকা জমিদারসহ সকল জমিদারদের প্রজাবিলিকৃত সম্পত্তিতে প্রজাদের মালিকানা অর্জন, রিটেইনেবল ৩৭৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমিতে জমিদারদের মালিকানা অর্জন এবং নন-রিটেইনেবল সম্পত্তিতে সরকারের মালিকানা অর্জন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন যে, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাইস্বত্ব আইন কার্যকরী হওয়ার পর সকল জমিদার ও প্রজাগণ যার যার স্ট্যাটাস পরিবর্তনে সরকারের অধীনে সাধারণ এক শ্রেণির রায়ত বা মালিক হিসেবে গণ্য হইয়া উভয়েই সরকারের সেরেস্তায় সমান হারে নামমাত্র খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে বেচা-বিক্রিসহ পরবর্তী ও স্থলবর্তীগণক্রমে যদৃচ্ছা ভোগ দখলের অধিকারী হন।
ইতঃপূর্বে উল্লিখিত ওইরূপ আইন এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনা সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয় মানিয়া নিয়া
যথাক্রমে- ২৭/১০/২০১৫ তারিখে ৩১.০০.০০০০. ০৪২.৬৭.০৩২.১৫ এবং ০২/০২/২০১৬ তারিখে ৩১.০০.০০০০.০৪৬. ৫৮.০১৯.১২-৭০ নং স্মারক ইস্যু করিয়া ১৯৫২ সনের প্রজাবিলিকৃত গেজেটে উল্লিখিত সম্পত্তিতে সরকারি সংস্থা কোর্ট অব ওয়ার্ডসকে মালিকানা দাবিতে সাধারণ প্রজাস্বত্বের মালিকদের হয়রানি করা হইতে বারিত করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোর্ট অব ওয়ার্ডসতে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ইতঃপূর্বে উল্লিখিত আইন, সর্বোচ্চ আদালতের রায় ও সরকারের নির্দেশনার বিপরীতে প্রজাবিলি গেজেটে উল্লিখিত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর সম্পত্তি হিসেবে অলীক দাবিতে লিজ দিয়া প্রজাইস্বত্বে মালিকদের পুনরায় হয়রানি শুরু করিলে প্রজাইস্বত্বে মালিকদের মধ্যে কতিপয় ক্ষুব্ধ মালিক উহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে যথাক্রমে আদালত অবমাননার মোকদ্দমা নং-২২৬/১৩ ও ৩৪৬/১৩ রুজু করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত অবমাননার মোকদ্দমাতে আদালত অবমাননার রুল ইস্যু করিয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজারকে সশরীরে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইতে বলিলে তৎকালীন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজার মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশিতমতে হাজির হইয়া হলফান্তে নিঃশর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ তাহাদের প্রার্থিত ক্ষমা গ্রহণ করিলেও তাহাদের এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেন যে, ভবিষ্যতে যদি প্রজাবিলি গেজেটে উল্লিখিত সম্পত্তিতে মালিকানা দাবিতে উহাতে উল্লিখিত কোনো সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর কোনো কর্মকর্তা লিজ বা অন্য কোনো প্রকারে হস্তান্তরের মাধ্যমে কোনো প্রজাইস্বত্বের মালিকদের হয়রানি করা হয়, তবে কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর সংশ্লিষ্ট উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর মাফ করা হইবে না।
৬) প্রজাইস্বত্বে সাধারণ জনগণের অর্জিত মালিকানাধীন সম্পত্তি, জমিদারদের রিটেইনেবল খাস সম্পত্তিতে অর্জিত মালিকানাধীন সম্পত্তি এবং নন-রিটেইনেবল সম্পত্তিতে সরকারের অর্জিত মালিকানাধীন সম্পত্তির পরবর্তী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন : উক্তরূপে এসএটি অ্যাক্টের বিধানমতে হোলসেল অধিগ্রহণ কার্যক্রমের মাধ্যমে জমিদারদের নন-রিটেইনেবল সম্পত্তিতে সরকারের মালিকানা অর্জিত সম্পত্তি এবং প্রজাগণের অর্জিত রায়তি স্বত্বের সম্পত্তি ও জমিদারদের রিটেইনেবল সম্পত্তিতে অর্জিত মালিকানাধীন সম্পত্তি পরবর্তীতে কীভাবে ভোগদখল, হস্তান্তর, রেকর্ড প্রস্তুত, নামজারি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হইবে তৎমর্মে উক্ত আইনের পঞ্চম খণ্ডে বর্ণিত হয়। পঞ্চম খণ্ডে বর্ণিত ধারাগুলোর মধ্যে ৭৯ ধারাতে বলা হয় যে, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের প্রেক্ষিতে ১ হইতে ৪র্থ খণ্ডের কার্যক্রম বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং শুধুমাত্র পঞ্চম খণ্ড তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য বলবৎ থাকবে। পঞ্চম খণ্ডে উল্লিখিত ৮১ ধারাতে বলা হয় যে, অদ্য হইতে পূর্বের জমিদার ও তাহাদের অধীনস্থ প্রজা উভয়েই সরকারের অধীনে সাধারণ প্রজা হিসেবে গণ্য হইবে এবং থাকিবে। উক্ত আইনের ৭৬ ধারাতে বলা হয় যে, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনের বিধান মতে সরকারের অর্জিত সম্পত্তি সরকার তাহার ইচ্ছামতো ভোগদখল বাদেও রেজিস্ট্রি লিজ দলিলের মাধ্যমে যেকোনো নাগরিকের বরাবরে লিজ দিতে পারিবেন। অন্যদিকে ৯৩ ধারাতে সাধারণ রায়ত বা নাগরিকের রায়তি স্বত্বে অর্জিত সম্পত্তি কোনোক্রমে অন্য রায়তি স্বত্বে মালিক বা নাগরিকের নিকট বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন না বা নতুনভাবে তার অধীনে প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি করিতে পারিবেন না মর্মে সুস্পষ্ট করেন। উক্ত আইনের ৮৯ ধারাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, কোনো রায়তি স্বত্বের জমির মালিক পরবর্তীতে অন্য প্রক্রিয়ায় মালিক তাহার জমি রেজিস্ট্রি দলিল ছাড়া কোনো প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। উক্ত আইনে ১৪৪ ধারাতে সরকার ও সাধারণ নাগরিকের মালিকানাধীন সম্পত্তির পরবর্তী রেকর্ড কীভাবে সরকার কর্তৃক প্রস্তুত ও প্রকাশ হইবে তৎবিষয়ে বর্ণিত হয়। চূড়ান্তভাবে প্রস্তুতকৃত রেকর্ড বা খতিয়ানে উল্লিখিত সম্পত্তি পরবর্তীতে ১১৭ ধারার বিধানমতে নামজারি ও জমাভাগের জন্য কাহার নিকট দরখাস্ত দিতে হইবে এবং তৎপর কাহার নিকট কত দিনের মধ্যে আপিল, রিভিশন ও রিভিউ ইত্যাদি রুজু করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে ধারা ১৪৬ হইতে ১৫০ তে বর্ণিত হয়। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-তে বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত আইন কার্যকরী করার সুবিধার্থে সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারের বিধি ও পরিপত্র গেজেট আকারে প্রস্তুত ও প্রকাশ করেন এবং তৎমতে বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।
পরিশেষে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে গড়ে তোলার সংগ্রামে ও জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন অভিমুখী যুগোপযোগী আমূল সংস্কার এখন সময়ের দাবি।
#

সৈয়দ আমিরুজ্জামান
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট;
বিশেষ প্রতিনিধি, সাপ্তাহিক নতুনকথা;
সম্পাদক, আরপি নিউজ;
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, জাতীয় কৃষক সমিতি;
সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, মৌলভীবাজার জেলা;
‘৯০-এর মহান গণঅভ্যুত্থানের সংগঠক ও সাবেক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী।
সাবেক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ খেতমজুর ইউনিয়ন।
সাধারণ সম্পাদক, মাগুরছড়ার গ্যাস সম্পদ ও পরিবেশ ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ আদায় জাতীয় কমিটি।
প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ আইন ছাত্র ফেডারেশন।